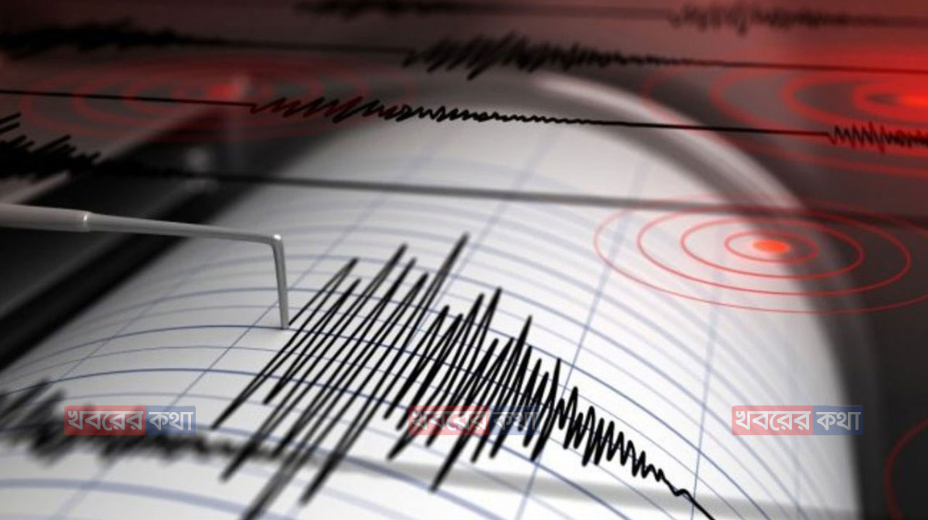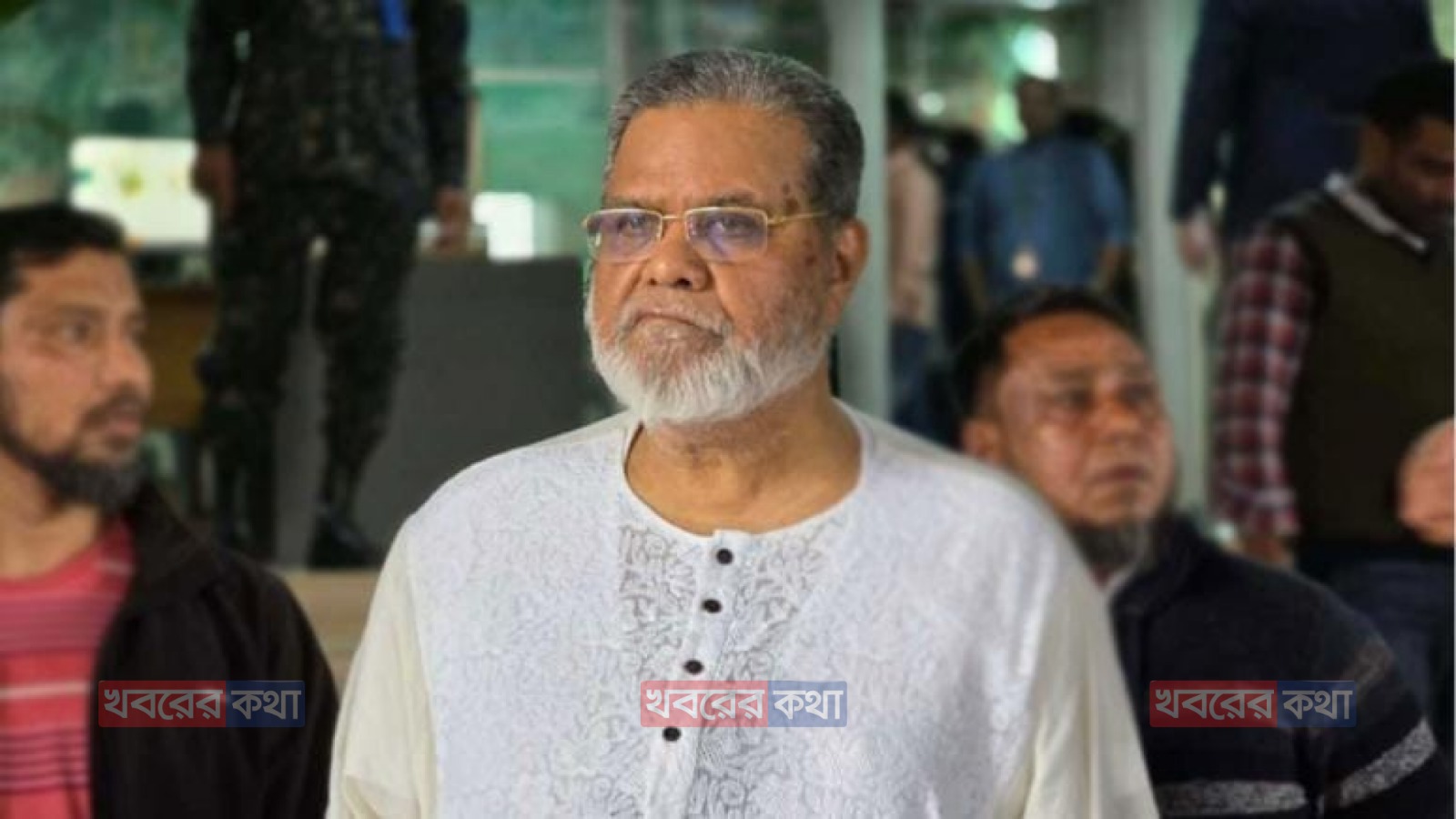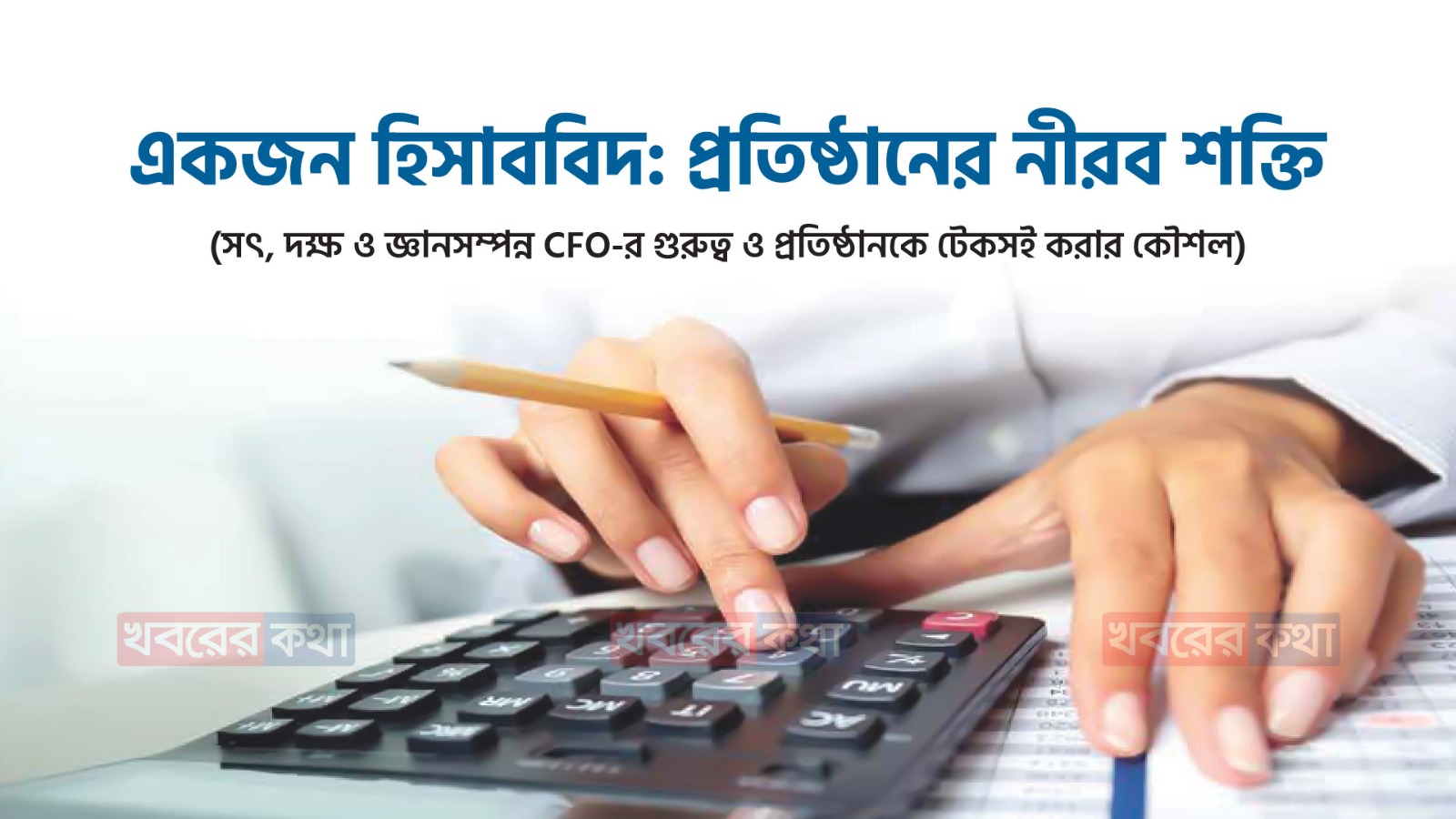“ফারাক্কার ফাঁদে বাংলাদেশ: বাঁধের পঞ্চাশ বছরের বেদনা ও বিপর্যয়।”
- আপডেট সময় ০৬:৩৪:৪০ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ১৬ মে ২০২৫
- / 478
আজ ঐতিহাসিক ফারাক্কা দিবস। ১৯৭৬ সালের এই দিনে ফারাক্কা ব্যারাজ অভিমুখে লংমার্চ করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া ফেলে দেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (1880-1976)। নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে এমন সোচ্চার জনমত ফারাক্কা লংমার্চ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনজীবন, কৃষি, পরিবেশ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। অথচ, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পার্শ্ববর্তী দেশের একতরফা পানি ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের অনেক নদ-নদী আজ বিলুপ্তপ্রায়। এমনই একটি করাল ছায়া বিস্তারকারী প্রকল্প হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ফারাক্কা বাঁধ। 1975 সালের 16 মে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ফারাক্কা ব্যারাজ, যার পরিণতিতে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশগত, কৃষিনির্ভর ও মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।
উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল পাকিস্তান আমলে 1952 সাল থেকে। তখন থেকে 1970 সাল পর্যন্ত তৎকালীন কর্তা ব্যক্তিরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেয়নি, ফলে ভারত তার-মতো কাজ করে গেছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত এই বাঁধটি একটি বৃহৎ জলনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হিসেবে ভারত সরকার কর্তৃক 1961 সালে অনুমোদিত হয়। নির্মাণ কাজ শুরু হয় 1963 সালে এবং শেষ হয় 1970-এর দশকের শুরুতে। বাঁধটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 2240 মিটার, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 109 টি গেট। এটি হুগলি নদীর প্রবাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি ডাইভারশন খালের মাধ্যমে গঙ্গার পানি পশ্চিম দিকে মোড় নেওয়ানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করা এবং পলিমাটি দ্বারা নদী মুখের ব্লকেজ ঠেকানো। কিন্তু এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের মত একটি স্বাধীন দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে একতরফাভাবে একটি আন্তঃসীমান্ত নদীতে এ প্রকল্প চালু করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত। 1975 সালের 16 মে ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়, বাংলাদেশের উদ্বেগ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে এটিকে স্থায়ী কার্যক্রম হিসেবে রূপ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই যখন দেশটি চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে ভারতের এই unilateral পদক্ষেপ দ্বিপক্ষীয় আস্থার ঘাটতির প্রমাণ। চালু হওয়ার কিছুদিন পরেই বাংলাদেশের পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ কমে আসতে শুরু করে। বর্ষাকালে কিছুটা প্রবাহ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারি থেকে মে মাস) পানি একেবারে সংকুচিত হয়ে আসে, যা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে।
বর্ষাকাল আসলেই শুনতে পাওয়া পাওয়া যায় বাংলাদেশের এই নদীর পানির প্রবাহ এত কিউসেক ঐ নদীর পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ইত্যাদি। এরমধ্যে কিউসেক শব্দটি নিয়ে অনেকে গুলিয়ে ফেলে। শুরুতেই কিউসেক শব্দটি ব্যাখ্যা করি, পরে গঙ্গা চুক্তি নিয়ে কথা বলব। অনেকে মনে করে থাকেন কিউসেক আয়তনের (Volume) একক। আসলে কিউসেক কখনো আয়তনের একক নয় বরং কিউসেক হল দুইটি রাশি যুক্ত করে তৈরি একটি যৌগিক একক (মৌলিক একক সাতটি)। কিউসেকের মধ্যে রয়েছে আয়তনের একক কিউবিক ফুট বা ঘনফুট (ft3) ও সময়ের একক সেকেন্ড(s)। সাধারণত নদীর প্রবাহ (Flow or Discharge) মাপার একটি জনপ্রিয় একক কিউসেক (USA প্রচলন করে)। এক সেকেন্ডে কত কিউবিক ফুট পানি কোনো বাঁধ বা জলাধার থেকে ছাড়া হল তা মাপা হয় কিউসেক দিয়ে। 1 কিউবিক ফুট মানে 28.317 লিটার। তার মানে, কোনও বাঁধ বা জলাধার থেকে 1 সেকেন্ডে 28.317 লিটার পানি ছাড়া হলে বলা যেতে পারে সেখান থেকে 1 কিউসেক হারে পানি ছাড়া হচ্ছে। আরও সহজ করে বললে, সাধারণ বালতিতে 30 লিটার পানি ধরে। অর্থাৎ আপনি যদি এক সেকেন্ডের মধ্যে যদি ওই বালতির পানি পুরোটা ঢালতে পারেন তাহলে বলা যেতে পারে আপনি 1 কিউসেকের কিছু বেশি পানি ঢাললেন।
Hydrologist-দের মতে, গঙ্গা চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ দিয়ে প্রবাহিত একটি আন্তর্জাতিক নদী; বাংলাদেশে পদ্মা (গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ) নামে পরিচিত। ভারতের হুগলী নদীতে পানি সরবরাহ এবং কলকাতা বন্দরটি সচল করার জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যার অবস্থান বাংলাদেশ থেকে 18 কিলোমিটার উজানে ভারতের ভূখণ্ডে গঙ্গা নদীর ওপরে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশে পানির প্রবাহ কমতে থাকার প্রেক্ষাপটে 1996 সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে 30 বছর মেয়াদি গঙ্গা চুক্তি হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে পানিবণ্টনের জন্য একটি সূচি নির্ধারিত হয়। গত চার দশকেরও বেশি সময়ে এই বাঁধ গঙ্গা অববাহিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে যার কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছে দুই দেশই। ভারত কোন মৌসুমে এই বাঁধের স্লুইস গেট বন্ধ রাখবে, কখন খুলে দেবে, সে বিষয়ে ফারাক্কা পানি বণ্টন চুক্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারত কী পরিমাণ পানি পাবে সেটা নির্ভর করবে উজানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, পানির প্রবাহ ও গতিবেগের ওপর। গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী, শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি থেকে 31শে মে পর্যন্ত দুই দেশ চুক্তিতে উল্লেখিত ফর্মুলা অনুযায়ী পানি ভাগাভাগি করে নেবে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, নদীতে 70 হাজার কিউসেক বা তার কম পানি থাকলে দুই দেশ সমান সমান পানি ভাগ করে নেবে। পানির পরিমাণ 70 হাজার কিউসেক থেকে 75 হাজার কিউসেক হলে 40 হাজার কিউসেক পাবে বাংলাদেশ। অবশিষ্ট প্রবাহিত হবে ভারতে। আবার নদীর পানির প্রবাহ যদি 75 হাজার কিউসেক বা তার বেশি হয় তাহলে 40 হাজার কিউসেক পানি পাবে ভারত। অবশিষ্ট পানি প্রবাহিত হবে বাংলাদেশে। তবে কোন কারণে যদি ফারাক্কা নদীর পানির প্রবাহ 50 হাজার কিউসেকের নীচে নেমে যায় তাহলে দুই দেশে কে কি পরিমাণ পানি পাবে সেটা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।
গঙ্গা তথা পদ্মা নদী থেকে কোন মৌসুমে কে কতো পানি পাবে অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারত যার যার ন্যায্য হিস্যা পেল কিনা সেটা এই জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে দুই দেশের নদী কমিশনের পর্যবেক্ষণ দল। বাংলাদেশে কী পরিমাণ পানি প্রবেশ করছে বা সরে যাচ্ছে সেটা পরিমাপ করা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে। অন্যদিকে ভারতের অংশে দৈনিক পানির প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করা হয় ফারাক্কা ব্যারেজের নীচে, ফিডার ক্যানেলে এবং ন্যাভিগেশন লকে। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষা মৌসুম জুড়ে পানি কী পরিমাণ আটকে রাখা হবে বা ছাড়া হবে সেটা নির্ভর করে ভারতের অংশে গড় বৃষ্টিপাত ও নদীর পানি প্রবাহের ওপর। ফারাক্কা বাঁধের সামনে যে পন্ড থাকে, সেখানে পানির উচ্চতা মাপার জন্য একটি রেকর্ডিং লেভেল থাকে যে এই পর্যন্ত পানি ধরে রাখলে বাঁধের কোন ক্ষতি হবে না।পানি ওই ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম করলেই তারা গেটগুলো একে একে খুলে দিয়ে পানি ছাড়তে থাকে। না হলে পুরো বাঁধ পানির তোড়ে ভেসে যাবে।
বাংলাদেশ যেহেতু ভাটির দেশ তাই সমুদ্রে যাওয়ার আগে সেই পানির ধাক্কাটা বাংলাদেশ ওপর দিয়েই যায়। এরপর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পন্ডে পানির লেভেল অনুযায়ী পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রতিবছর বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফারাক্কা বাঁধ সরিয়ে স্থায়ী সমাধান চেয়ে আসছেন। একই দাবি বাংলাদেশের পরিবেশবাদীদেরও। কেননা এই বাঁধের কারণে বর্ষার মৌসুমে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের বেশ কিছু জেলাও বন্যা ও নদী ভাঙনের কবলে পড়ে। এতে শুষ্ক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। কেননা শুষ্ক মৌসুমে পদ্মার পানি শুকিয়ে পলি জমতে থাকে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে উভয় দেশেই কিছু নদী তার স্বাভাবিক গতি আর নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। অনেক নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমতে জমতে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে এতে নদীর খাড়িগুলোর পানি পরিবহণ ক্ষমতা কমে গেছে। এজন্য বন্যা ঠেকানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে গ্রীষ্ম মৌসুমে ভারত পানি আটকে রাখায় বাংলাদেশ প্রয়োজনের সময় পানি পাচ্ছে না। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে কৃষিজমি, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন সর্বোপরি আবহাওয়ার ওপর। যা পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনছে। পদ্মার অন্যান্য শাখা নদীও এ কারণে পানি সংকটের মুখে পড়েছে। এই বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পরিবেশগত ক্ষতি, কৃষি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং জনস্বাস্থ্য ও মানবিক বিপর্যয় সমূহ হলো-
১. নদী শুকিয়ে যাওয়া ও নাব্যতা হ্রাস: পদ্মাসহ বহু শাখা নদী যেমন বড়াল, আত্রাই, মরা পদ্মা, করতোয়া, মহাকুমার জলাধারগুলো ফারাক্কা চালুর পর শুকিয়ে যেতে থাকে। নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বহু খাল-বিল ও জলাভূমি হারিয়ে গেছে।
২. নদীভাঙন ও ভৌগোলিক পরিবর্তন: নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় ব্যাপক নদীভাঙন শুরু হয়, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও পাবনা জেলায়। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। বর্ষাকালে হঠাৎ করে বাঁধের গেট খুলে দিলে বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা বেড়ে যায়।
৩. জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস: জলজ প্রাণী যেমন দেশীয় মাছ, কচ্ছপ, শাপলা-শালুক সহ অসংখ্য জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে। পদ্মা নদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ‘হিলশা মাছ’, যা এখন উপরিভাগে অনেকাংশে বিলুপ্ত। একইভাবে পাখির আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় অভিবাসী পাখির সংখ্যা কমে গেছে।
৪. সেচের পানির সংকট: উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের চাষাবাদ নির্ভর করে পদ্মা ও তার শাখা নদীর পানির উপর। কিন্তু গ্রীষ্মকালে পানির প্রবাহ এত কমে যায় যে অনেক কৃষক সেচের পানির জন্য নির্ভর করতে বাধ্য হন গভীর নলকূপ বা ডিজেলচালিত পাম্পের উপর। এতে সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়।
৫. ফসলের উৎপাদন হ্রাস: কৃষকদের অভিযোগ, ফারাক্কা চালুর আগে যেখানে বছরে তিনবার ফসল ফলানো সম্ভব হতো, এখন তা কমে এসেছে এক বা দুইবারে। বোরো মৌসুমে ধান চাষে পানি সংকটে অনেক জমি অনাবাদি থাকে।
৬. মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া: পানি না থাকার ফলে পলি পড়া কমে যায়, ফলে নদীতীরবর্তী অঞ্চলের মাটি হারাচ্ছে তার উর্বরতা। এক সময় যে মাটি ছিল সোনালি, তা এখন অনুর্বর ও ধুলোময়।
৭. পানিবাহিত রোগের প্রকোপ: পানির সংকটে মানুষ পুকুর, খাল, জলাশয় থেকে অপরিশোধিত পানি ব্যবহার করছে, যার ফলে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। শিশুমৃত্যুর হার এসব অঞ্চলে তুলনামূলক বেশি।
৮. পানির জন্য হাহাকার: বিশেষ করে রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও কুষ্টিয়ার মানুষ শুষ্ক মৌসুমে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানির অভাবে দুর্ভোগে পড়ে। নারী ও শিশুদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে পানি আনতে হয়।
৯. জলবায়ু উদ্বাস্তু: নদীভাঙন ও পানির অভাবে বহু মানুষ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু’। রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানে এদের অস্তিত্ব অনেক সময় ঠাঁই পায় না।
নদী কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, শুষ্ক মৌসুমে কখনোই নির্ধারিত পরিমাণ পানিও বাংলাদেশে আসেনি। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তির কারণে পানিবণ্টন প্রশ্নে সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। বাংলাদেশ সরকার 1977 সাল থেকেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্থাপন করেছে। জাতিসংঘ, সাউথ এশিয়ান রিভারস কমিশন, ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামসহ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কার্যকর কোনো সমাধান আসেনি। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, যেমন BUET, WARPO, IUCN এবং আন্তর্জাতিক গবেষকগণ ফারাক্কা বাঁধকে বাংলাদেশের জন্য এক “Slow Poison” হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ বাঁধকে কেন্দ্র করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার পানিবণ্টনের যৌথ ব্যবস্থাপনার দাবি উঠেছে বহুবার। সবমিলিয়ে ফারাক্কা বাঁধ শুধুমাত্র একটি পানি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প নয়, এটি হয়ে উঠেছে সীমান্তের এপারের মানুষের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি দুঃস্বপ্ন। পরিবেশ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ও মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রে ফারাক্কার প্রভাব সুস্পষ্ট।
গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যৎ আরও ভয়াবহ হতে পারে। জলসীমান্তের এই সংকট শুধু রাষ্ট্রের দায় নয়, এটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশ ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ফারাক্কা সমস্যার একটি টেকসই ও ন্যায্য সমাধান সময়ের দাবি।